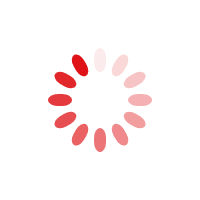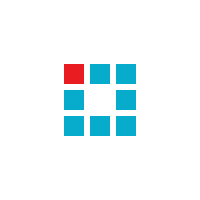
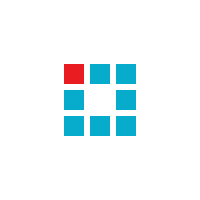
প্রশ্নঃ ' সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন। হউক দূর অকল্যান সকল অশোভন।' --- চরণ দুটি কার লেখা?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
শেখ ফজলল করিম (৯ এপ্রিল ১৮৮২/বাংলা ৩০শে চৈত্র ১২৮৯ - ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) একজন স্বনামধন্য বাঙালি সাহিত্যিক। তার লেখা কবিতার কয়েকটি লাইন,
কোথায় স্বর্গ?
কোথায় নরক?
কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক
মানুষেতে সুরাসুর

প্রশ্নঃ যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না -----
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
অকালের ফুল অকালকুসুম
অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে কাজ করে যে অবিমৃশ্যকারী
অনুমান করা যায় না যা অননুমেয়
অরিকে দমন করে যে অরিন্দম
অশ্ব,রথ,হস্তী,ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার চতুরঙ্গ
অগ্রে দান করে যে অগ্রদানী
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক অনুসন্ধিৎসু
অপকার করার ইচ্ছা অপচিকীর্ষা

প্রশ্নঃ ' অপমান' শব্দের ' অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
‘উপসর্গ’ কথাটির মূল অর্থ ‘উপসৃষ্ট’। এর কাজ হলো নতুন শব্দ গঠন করা। উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই, তবে এগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। মনে রাখতে হবে, উপসর্গ সব সময় মূল শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়

প্রশ্নঃ ' সোনালী কাবিন ' এর রচয়িতা কে?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
সোনালী কাবিন ' এর রচয়িতা আল মাহমুদ
‘সোনালী কাবিন’ আল মাহামুদের সনেট জাতীয় কাব্য। আল মাহমুদ যে সকল সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে সোনালী কাবিন তাকে বেশি পরিচিতি প্রদান করেছে। এতে মোট ১৪টি সনেট রয়েছে।
‘‘সোনার দিনার নেই, দেনেমাহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু’টি,
আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনোকালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রুকুটি;
ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,
ছলনা জানি না বলে আর কোনো ব্যবসা শিখিনি;
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখী, যেই পণ্যে অলংকার কিনি।
বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরুষ আবৃত করে জলপাইয়ের পাতাও থাকবে না;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিয়ো সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হব চিরচেনা
পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা;
দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।”
মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ (১১ জুলাই ১৯৩৬ – ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) যিনি আল মাহমুদ নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্প লেখক, শিশুসাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে সক্রিয় থেকে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনায় ও বাক্ভঙ্গীতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে । তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সরকার বিরোধী সংবাদপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ (১৯৭২-১৯৭৪) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
১৯৫০-এর দশকে যে কয়েকজন লেখক বাংলা ভাষা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তাদের মধ্যে মাহমুদ একজন। লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। কবি আল মাহমুদ তার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসের জন্যও খ্যতি অর্জন করেছিলেন।
আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তার পিতার নাম মীর আবদুর রব ও মাতার নাম রওশন আরা মীর। তার দাদার নাম আব্দুল ওহাব মোল্লা যিনি হবিগঞ্জ জেলায় জমিদার ছিলেন।
কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাই স্কুল এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়ালেখা করেন। মূলত এই সময় থেকেই তার লেখালেখির শুরু। আল মাহমুদ বেড়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলি, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রমুখের সাহিত্য পাঠ করে ঢাকায় আসার পর কাব্য সাধনা শুরু করেন এবং ষাট দশকেই স্বীকৃতি ও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন।
সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে ১৯৫৪ সালে মাহমুদ ঢাকা আগমন করেন। সমকালীন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র/পত্রিকার মধ্যে কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাফেলা পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে পদচারণা শুরু করেন। ১৯৫৫ সাল কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলা পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।
১৯৭১ সালে তিনি ভারত গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। যুদ্ধের পরে দৈনিক গণকণ্ঠ নামক পত্রিকায় প্রতিষ্ঠা-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। সম্পাদক থাকাকালীন এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।
১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গল্প লেখার দিকে মনোযোগী হন। ১৯৭৫ সালে তার প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ পানকৌড়ির রক্ত প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি পরিচালক হন। পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।
১৯৫৪ সাল অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে তার কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকা এবং কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, ময়ূখ ও কৃত্তিবাস ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে তার নাম পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর (১৯৬৩) সর্বপ্রথম তাকে স্বনামধন্য কবিদের সারিতে জায়গা করে দেয়। এরপর কালের কলস (১৯৬৬), সোনালি কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে উঠো (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থগুলো তাকে প্রথম সারির কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৯৩ সালে বের হয় তার প্রথম উপন্যাস কবি ও কোলাহল।
তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে তার কবিতায় অবলম্বন করেন। নারী ও প্রেমের বিষয়টি তার কবিতায় ব্যাপকভাবে এসেছে। উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হিসেবে নারীর যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের লালসাকে তিনি শিল্পের অংশ হিসেবেই দেখিয়েছেন আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তার অনন্য কীর্তি।
১৯৬৮ সালে ‘লোক লোকান্তর’ ও ‘কালের কলস’ নামে দুটি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তার সবচেয়ে সাড়া জাগানো সাহিত্যকর্ম সোনালি কাবিন। ১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধ তার কবিতায় বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস উৎকীর্ণ হতে থাকে; এর জন্য তিনি প্রগতিশীলদের সমালোচনার মুখোমুখি হন। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস “কবি ও কোলাহল”। কোনো কোনো তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিশ্বাসগ্রস্ততার কারণে তার বেশকিছু কবিতা লোকায়তিক সাহিত্যদর্শন দৃষ্টান্তবাদ দ্বারা অগ্রহণযোগ্য। তবে একথাও সত্য, কবিতায় দর্শন থাকে, কিন্তু দর্শন দ্বারা কবিতা নিয়ন্ত্রিত নয়, কবিতা আবেগের কারবার।

প্রশ্নঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
বসন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি ঋতুনাট্য। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ ফাল্গুন নাটকটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি একটি পালাগান এবং নাটকের আঙ্গিকে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পালাগান। এটি কবির প্রথম ঋতুনাট্যও বটে। নাটকের বিষয়বস্তু বসন্তের আগমন ও বিদায়। নাটকে ব্যবহৃত গানগুলি গীতবিতান গীতিসংকলনের প্রকৃতি পর্যায়ের বসন্ত উপপর্যায়ের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি উৎসর্গ করেন কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দেশ্যে। পরে এই নাটকটি ঋতু-উৎসব (১৯২৬) সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়।

প্রশ্নঃ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম----
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ বাংলা একাডেমি থেকে যে ৬ টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 'উত্তরাধিকার' একটি। প্রথমে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলে ও ১৯৮৩ সালে তা ত্রৈমাসিক করা হয়। বর্তমানে আবারও 'উত্তরাধিকার' মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, 'লোকায়েত' আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পাদিত পত্রিকা।

প্রশ্নঃ 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন----
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন, মুসলিম হলের ছাত্র এ.এফ.এম আবদুল হক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখের ওপর। এরাই ছিলেন প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য। নেপথ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করতেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর

প্রশ্নঃ ' ঠক চাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
আলালের ঘরের দুলাল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সফল উপন্যাস।প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৭ সালে এটি রচনা করেন

প্রশ্নঃ ' বঙ্গদর্শন ' পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
বঙ্গদর্শন উনিশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বা সাময়িকপত্র। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ, বারো এপ্রিল) তারিখে মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সে সময়ে অবিভক্ত বাংলায় কোনো উন্নত মানের সাময়িকপত্র ছিল না। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস অবধি এর সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে এর প্রকাশ স্থগিত থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত ৪টি সংখ্যার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ে ৫ বৎসর প্রকাশিত হয়।

প্রশ্নঃ ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল পার্থক্য ------
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরন। সাধারণত একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে অভিনয় করে নাটক পরিবেশিত হয়ে থাকে। নাটক লেখা হয় অভিনয় করার জন্য। তাই নাটক লেখার আগেই তার অভিনয় করার যোগ্য হতে হয়। নাটকে স্থান, সময় ও পরিবেশের বর্ণনা ছাড়াও সংলাপ লেখা থাকে। সংলাপ বলেই একজন অভিনেতা নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে বলে থাকেন। তবে সংলাপই শেষ কথা নয়। সংলাপবিহীন অভিনয়ও নাটকের অংশ।
সাধারণ মানুষের মধ্যে গল্পে গল্পে যে নাটক গড়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের গল্প অবলম্বন করে যার কাহিনি আবর্তিত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কথ্যরীতিতে যে নাটক বেঁচে থাকে তাই লোকনাট্য।
সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাদের মতে কাব্য দুই প্রকার - দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্য কাব্য এবং এটি সকল প্রকার কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ -
| “ | কাব্যেষু নাটকং রম্যম্। | ” |
নাটক দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত করে তোলে। রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় পরিস্ফুট হয় না। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাদের অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণসঞ্চার করেন, তাকে বাস্তব রূপৈশ্বর্য্য দান করেন। নাটকে অনেক সময় পাত্র-পাত্রীদের কথায় নাট্যকার নিজের ধ্যান-ধারণার কথাও সংযোগ করে দেন। এইজন্য এটি সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা অবজেকটিভস্ না-ও হতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নিজেকে যথাসাধ্য গোপনে রাখেন এবং তার চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ একটি নির্লিপ্ততা বর্তমান থাকে।
সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ পূর্বরঙ্গ বা মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়তঃ সভাপূজা (সামাজিকগণের), তৃতীয়তঃ কবিসংজ্ঞা বা নাটকীয় বিষয়-কথন এবং তারপর প্রস্তাবনা। 'মঙ্গলাচরণে' সূত্রধর (তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অভিনয়-পটু) রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থেকে অভিনয়-কার্য্যের বিঘ্নপরিসমাপ্তির জন্য যে মঙ্গলাচরণ করেন তার নাম 'নান্দী'।
প্রস্তাবনার পর সাধারণতঃ প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়। নাটকীয় কুশীলবগণ 'সূচিত' না হয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে পারে না। শুধু নায়ক বা আর্ত্ত যে-কোন চরিত্রের প্রবেশের জন্য সূচনার প্রয়োজন নেই। নাটকের ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হয়। তবে, সংস্কৃত নাটকে বিদ্বানপুরুষ সাধারণতঃ সংস্কৃত, বিদুষী মহিলাগণ শৌরসেনী, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠিগণ অর্দ্ধমাগধী, বিদূষক প্রাচ্যা এবং ধূর্ত্ত অবন্তিক ভাষা ব্যবহার করতেন।
সনাতনপন্থী নাট্যকারগণ নাটকে তিনটি ঐক্যনীতি মেনে চলতেন। সেগুলো হলোঃ-
ইংরেজি সাহিত্যে বেন জনসন ঐক্যনীতি মেনে চলেছেন এবং শেক্সপিয়ার মাত্র দ্য টেম্পেস্ট এবং দ্য কমেডি অব এরর'স-এ এই নিয়ম মেনে চলেছেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে কাল, স্থান ও ঘটনার ঐক্য অনুঃসৃত হয়নি। ভবভূতির 'মহাবীর চরিত্রে' দ্বাদশবর্ষের ঘটনা নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়েছে। চরিত্রে দ্বাদশবর্ষের ঘটনা নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়েছে।
নাটকের শ্রেণীবিভাগ কোনো বিশেষ বিষয়কে ভিত্তি করে করা হয়নি। নানারকম বিষয়বস্তু অনুসারে নাটককে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। নাটকের শ্রেণীবিভাগগুলো এরকম: ক) ভাব সংবেদনা রীতি অনুসারে (০১) ট্রাজেডি (০২) কমেডি (০৩) ট্রাজি-কমেডি (০৪) মেলোড্রামা ও (০৫) ফার্স।
খ) বিষয়বস্তুর উৎসরীতি অনুসারে (০১) পৌরাণিক (০২) ঐতিহাসিক (০৩) ঐতিহাসিককল্প চরিত্রমূলক (০৪ ) সামাজিক (০৫) পারিবারিক (০৬) উপকথাশ্রয়ী ও (০৭) কাল্পনিক
গ) বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে (০১) ধর্মমূলক (০২) নীতিমূলক (০৩) আধ্যাত্মিক (০৪) রাজনৈতিক (০৫) অর্থনৈতিক (০৬) প্রেমমূলক (০৭) দেশপ্রেমমূলক (০৮) সমাজরীতিমূলক (০৯) ষড়যন্ত্রমূলক (১০) রোমাঞ্চকর দুঃস্বাহসমূলক ও (১১) অপরাধ আবিষ্কারমূলক প্রভৃতি
ঘ) উপাদানযোজনা বৈশিষ্ট্য অনুসারে (০১) গীতিনাট্য বা অপেরা (০২) যাত্রা (০৩) নৃত্যনাট্য (০৪) নাটক বা ড্রামা
ঙ) আয়তন বা অঙ্কসংখ্যা অনুসারে (০১) মহানাটক (০২) নাটক (০৩) নাটিকা (০৪) একাঙ্কিকা
চ) গঠন রীতি অনুসারে (০১) ক্লাসিক্যাল (০২) রোমান্টিক (০৩) দৃশ্যাবলী
ছ) রচনারীতি অনুসারে (০১) পদ্যনাটক (০২) গদ্যনাটক (০৩) গদ্য-পদ্যময় নাটক
জ) উপস্থাপনারীতি অনুসারে (০১) বাস্তবিক নাটক (০২) ভাবতান্ত্রিক নাটক (০৩) রূপক নাটক (০৪) সাংকেতিক নাটক (০৫) এক্সপ্রেশানিস্টিক নাটক
ঝ) উদ্দেশ্য অনুসারে (০১) ঘটনামূখ্য (মোলোড্রামা) (০২) চরিত্রমূখ্য (চরিত্রনাট্য) (০৩) রসমূখ্য (রসনাট্য) ও (০৪) তত্ত্বমূখ্য (তত্ত্বনাটক)
সাধারণ মানুষের মধ্যে গল্পে গল্পে যে নাটক গড়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের গল্প অবলম্বন করে যার কাহিনি আবর্তিত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কথ্যরীতিতে যে নাটক বেঁচে থাকে তাই লোকনাট্য।

প্রশ্নঃ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য ------
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য: বাংলা ভাষার দুটি রূপ—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। দুটি রূপের মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্যও রয়েছে। নিচে এ দুয়ের পার্থক্য আলোচনা করা হলো।
| সাধু ভাষা |
চলিত ভাষা |
| ১। যে ভাষায় সাধারণত সাহিত্য রচিত হয় এবং যা মার্জিত ও সর্বজনস্বীকৃত, তাই সাধু ভাষা। | ১। শিক্ষিত লোক সাধারণ কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তা-ই চলিত ভাষা। |
| ২। সাধু ভাষা ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসারী। | ২। চলিত ভাষার সুনির্ধারিত ব্যাকরণ আজও তৈরি হয়নি। |
| ৩। সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী। | ৩। চলিত ভাষা সহজ ও স্বাভাবিক। এ ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশে উপযোগী। |
| ৪। সাধু ভাষার কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়। | ৪। চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল। |
| ৫। সাধু ভাষা কৃত্রিম। | ৫। চলিত ভাষা কৃত্রিমতা-বর্জিত। |
| ৬। সাধু ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতায় তেমন উপযোগী নয়। | ৬। চলিত ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতায় বেশ উপযোগী। |
| ৭। সাধু ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনাম পদগুলো সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে। যেমন—খাইতেছি, তাহারা ইত্যাদি। | ৭। চলিত ভাষায় ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদগুলো সংক্ষিপ্ত। যেমন—খাচ্ছি, তারা ইত্যাদি। |
| ৮। এ ভাষা প্রাচীন। | ৮। এটি আধুনিক। |
| ৯। সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি। | ৯। চলিত ভাষায় অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি। |
| ১০। সাধু ভাষায় অপনিহিত ও অভিশ্রুতির ব্যবহার নেই। | ১০। চলিত ভাষায় এদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। |
নিচে উল্লিখিত নিয়মগুলো অনুসরণ করে সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়:
উদাহরণ:
সাধুরীতি: দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির ওপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে!
চলিতরীতি: দেখলাম, এ সতেরো বছরের মেয়েটির ওপরে যৌবনের সমস্ত আলো এসে পড়েছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল থেকে সে জেগে ওঠেনি। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের ওপর সকালের আলো ঠিকরে পড়েছে, কিন্তু বরফ এখনো গলল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে!

প্রশ্নঃ ' সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন -----
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
দিগদর্শন (১৮১৮)
দিগদর্শন প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র।
শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।
চার পৃষ্ঠার পত্রিকাটি ছিল বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক পত্রিকা। এখানে বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ একসঙ্গে প্রকাশিত হত। শ্রীরামপুরের সাংবাদিকেরা একটি নিজস্ব ভাষারীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা এবং এখানে ছাত্রদের উপযোগী ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা রচনা থাকত।

প্রশ্নঃ 'প্রভাত চিন্তা ', 'নিভূত চিন্তা', 'নিশীত চিন্তা' প্রভূতি গ্রন্থের রচয়িতা ------
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
কালীপ্রসন্ন ঘোষ (জুলাই ২৩, ১৮৪৩ - অক্টোবর ২৯, ১৯১০) ছিলেন একজন বাঙালী সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, সাংবাদিক ও বাগ্মী।
১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই ঢাকা বিভাগের বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে তার জন্ম। তার পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। ১৯১০ সালের ২৯ অক্টোবর তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন।
বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগ্মিতার পরিচয় দেন। মাত্র বিশ বছর তখন তিনি কলকাতার ভবানীপুরে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এরপর থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।
তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য। তিনি তার সাংবাদিক জীবন শুরু করেন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত "ঢাকা শুভসাধিনী সভার" মুখপত্র "শুভসাধিনী" সম্পাদনার মাধ্যমে। এ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন ঢাকার ব্রাহ্মযুবকদের জন্য। ৪ বছর পর ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সম্পাদনা করেন সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা "বান্ধব"।
বাইশ বছর বয়সে ১৮৬৫ সালে ঢাকার নিম্ন আদালতে পেশকার হিসেবে কালীপ্রসন্ন ঘোষের কর্মজীবন শুরু হয়। এখানে এগারো বছর চাকরি করার তিনি ভাওয়াল এস্টেটের প্রধান দেওয়ান হিসেবে যোগ দেন এবং তিনি ভাওয়ালের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর যুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি ‘সাহিত্য-সমালোচনী সভা’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। কালীপ্রসন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সদস্য (১৮৯৪) এবং সহ-সভাপতির (১৮৯৭-১৯০০) পদ অলঙ্কৃত করেন। এছাড়াও তিনি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এবং সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতির মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালন করেন।
কালীপ্রসন্ন মূলত দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে লিখতেন।
এ ছাড়া "সঙ্গীতমঞ্জরী" (১৮৭২) নামে একখানা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতসংগ্রহ এবং "কোমল কবিতা" (১৮৮৮) নামে একখানা শিশুপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।
কালীপ্রসন্নের রচনারীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরেজ পন্ডিত কার্লাইলের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। তার রচনাসমূহ ভাবগাম্ভীর্য, ইতিহাসচেতনা ও গভীর জীবনবোধেপূর্ণ।
ইংরেজ সরকার তাকে পান্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৯৭ সালে "রায়বাহাদুর" এবং ১৯০৯ সালে "সিআইই" উপাধি প্রদান করে। বাংলার পণ্ডিতগণ তাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে অভিষিক্ত করেন।

প্রশ্নঃ ' সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' এই উক্তিটি কার?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
প্রমথ চৌধুরী (৭ আগস্ট ১৮৬৮ — ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রাবন্ধিক, কবি ও লেখক। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি বাংলা গদ্যে চলিতরীতির প্রবর্তক; এছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। সবুজপত্র পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতি প্রবর্তন করেন। গল্পকার ও সনেটকার হিসেবেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।
প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রাস ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ এ পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৮৯খ্রি বিএ(অনার্স)দর্শন, ১৮৯০সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন ।
প্রমথ চৌধুরী কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করেন । কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে পড়ান । তিনি ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এছাড়াও তিনি মাসিক সবুজপত্র ও বিশ্বভারতী সম্পাদনা করেন।রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৪২-১৯২৩) কন্যা ইন্দিরা দেবীর (১৮৭৩-১৯৬০) সহিত তাহার বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি জামাই। লেখক আশুতোষ চৌধুরী(১৮৮৮-১৯৪৪) সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ। রবীন্দ্রনাথের ভগিনী প্রতিভা দেবীর সহিত আশুতোষ চৌধুরী বিবাহ হয়।
তার সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল। তার সম্পাদিত সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে আগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তার প্রবর্তিত গদ্যরীতিতে “সবুজ পত্র” নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তারই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে ইতালিয় সনেট এর প্রবর্তক।

প্রশ্নঃ শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন -----
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
মুহুর্মুহু /অব্যয় পদ/ বারংবার।

প্রশ্নঃ দ্যুলোকে শব্দের যথার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
সন্ধি: সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন- আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (া) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (া) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে =তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্ম হয়েছে।
সন্ধির উদ্দেশ্য
(ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং
(খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন- কচু + আদা + আলু =কচ্চাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচ্চান্বাদা হয় না।
বাংলা শব্দের সন্ধি
বাংলা সন্ধি দুই রকমের:
১. স্বরসন্ধি
২. ব্যঞ্জনসন্ধি।
১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।
১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত ঘরের একটির লোপ হয়। যেমন-
| (ক) অ + এ = এ (অ লােপ) | যেমন – শত + এক = শতেক। | এরূপ – কতেক। |
| (খ) আ + আ = আ (একটি আ লােপ)। | যেমন – শাঁখা + আরি = শাঁখারি। | এরূপ – রুপা + আলি = রূপালি। |
| (গ) আ + উ = উ (আ লােপ)। | যেমন – মিথ্যা + উ = মিথুক। | এরূপ – হিংসুক, নিন্দুক ইত্যাদি। |
| (ঘ) ই + এ = ই (এ লােপ)। | যেমন – কুড়ি + এক = কুড়িক। | এরূপ – ধনিক, গুটিক ইত্যাদি। |
| আশি + এর = আশির (এ লােপ)। | এরূপ — নদীর (নদী +এর)। |
২. কোনাে কোনাে স্থলে পাশাপাশি দুটি ঘরের শেষেরটি লােপ পায়। যেমন – যা + ইচ্ছা + তাই =যাচ্ছেতাই। এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লােপ পেয়েছে।
২। ব্যঞ্জন সন্ধি
সরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর সরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)- এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।
১. প্রথম ধ্বনি অঘােষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘােষ হলে, দুটি মিলে ঘােষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘােষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘােষ ধ্বনিও ঘােষ হয়। যেমন – ছােট + দ =ছােড়দা।
২. হলন্ত র (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে রু লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়।
যেমন—
| আর + না = আন্না | ধর, + না =ধন্না |
| চার + টি = চাট্টি | দুর, + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি। |
৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লােপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির
দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন-
| নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত্ + জ = জ্জ) |
| বদ্ + জাত = বজ্জাত |
| হাত + ছানি = হাচ্ছানি ইত্যাদি। |
৪. ‘প’-এর পরে ‘চ’ এবং “স’-এর পরে ‘ত এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন –
| পাঁচ + শ = পাশ |
| সাত + শ = সাশ |
| পাঁচ + সিকা = পাশিকা |
৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে ঘরের লােপ হয় না। যেমন –
| বােন + আই =বােনাই | বার + এক =বারেক |
| চুন + আরি =চুনারি | তিন + এক =তিনেক |
| তিল + এক = তিলেক |
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন –
| কঁচা + কলা = কাঁচকলা | ঘােড়া + দৌড় = ঘােড়দৌড় |
| নাতি + বৌ = নাতবৌ | ঘােড়া + গাড়ি = ঘােড়গাড়ি ইত্যাদি। |
তৎসম শব্দের সন্ধি
বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার:
(১) স্বরসন্ধি
(২) ব্যঞ্জন সন্ধি
(৩) বিসর্গ সন্ধি
১. স্বরসন্ধি
স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।
১. অ-কার কিংবা আকারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-
| অ + অ = আ | নর+ অধম = নরাধম | এরূপ- হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি |
| অ + আ = আ | হিম + আলয় = হিমালয়। | এরূপ – দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি। |
| আ + অ = আ | যথা + অর্থ = যথার্থ। | এরূপ — আশাতীত, কথামৃত, মহার্ঘ ইত্যাদি। |
| আ + আ = আ | বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়। | এরূপ- কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি। |
২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—
| অ + ই = এ | শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা। |
| আ + ই = এ | যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট। |
| অ + ঈ = এ | পরম + ঈশ =পরমেশ। |
| আ + ঈ = এ | মহা + ঈশ =মহেশ। |
| এরূপ –পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি। | |
৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন-
| অ + উ = ও | সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়। |
| আ + উ = ও | যথা + উচিত = যথােচিত। |
| অ + ঊ = ও | গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহাের্ধ্ব। |
| আ + ঊ = ও | গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি। |
| এরূপ — নীলােৎপল, চলাের্মি, মহােৎসব, নবােঢ়া, ফলােদয়, যথােপযুক্ত, হিতােপদেশ, পরােপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি। | |
৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর’ হয় এবং তা রেফ () রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন—
| অ + ঋ = অ | দেব + ঋষি = দেবর্ষি। |
| আ + ঋ = অর | মহা + ঋষি = মহর্ষি। |
| এরূপ — অধমর্ণ, উত্তমর্ণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি। | |
৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ‘ঋত’-শব্দ থাকলে (অ, আ+ঋ) উভয় মিলে ‘আর’ হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন—
| অ + ঋ = আর | শীত + ঋত = শীতার্ত। |
| আ + ঋ = আর | তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত। |
| এরূপ —ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি। | |
৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—
| অ + এ = ঐ | জন + এক = জনৈক। |
| আ + এ = ঐ | সদা + এব = সদৈব। |
| অ + ঐ = ঐ | মত + ঐক্য = মতৈক্য। |
| আ + ঐ = ঐ | মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য। |
| এরূপ- হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি। | |
৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-
| অ+ ও = ঔ | বন + ওষধি = বনৌষধি। |
| আ + ও = ঔ | মহা + ওষধি = মহৌষধি। |
| অ + ঔ = ঔ | পরম + ঔষধ = পরমৌষধ। |
| আ + ঔ = ঔ | মহা + ঔষধ = মহৌষধ। |
৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-
| ই + ই = ঈ | অতি + ইত = অতীত |
| ই + ঈ = ঈ | পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা। |
| ঈ + ই = ঈ | সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র। |
| ঈ + ঈ = ঈ | সতী + ঈশ = সতীশ। |
| এরূপ- গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথ্বীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি। | |
৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য ঘর থাকলে ই বা ঈ স্থানে ‘য বা য() ফলা হয়। য-ফলা।
লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন-
| ই + অ = + অ | অতি + অন্ত = অত্যন্ত। |
| ই + আ = ঘৃ + আ | ইতি + আদি = ইত্যাদি। |
| ই + উ = খৃ + উ | অতি + উক্তি = অত্যুক্তি। |
| ই + উ = য + উ | প্রতি + ঊষ = প্রত্যুষ। |
| ঈ + আ = + আ | মসী + আধার = মস্যাধার। |
| ই + এ = য + এ | প্রতি + এক = প্রত্যেক। |
| ঈ + অ = ঘৃ + অ | নদী + অ = নদঘু। |
| এরূপ-প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি। | |
১০. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়; উ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন—
| উ + উ = উ | মরু + উদ্যান = মরুদ্যান। |
| উ + উ = উ | বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব। |
| ঊ + উ = উ | বধূ + উৎসব = বধূৎসব। |
| ঊ + উ = উ | ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব। |
১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার ও উ-কার ভিন্ন অন্য ঘর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন-
| উ + অ = ব + অ | সু + অল্প = স্বল্প |
| উ + আ = ব + আ | সু + আগত = স্বাগত |
| উ + ই = ব + ই | অনু + ই = অন্বিত |
| উ + ঈ = ব + ঈ | তনু + ঈ = তন্বী |
| উ + এ = ব + এ | অনু + এষণ = অন্বেষণ |
| এরুপ- পশ্বধম, পশ্বাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি। | |
১২. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব ও আবু হয়। যেমন-
| এ + অ = অহ্ + অ | নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন। |
| ঐ + অ = আয়ু + অ | নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক। |
| ও + অ = অব + অ | পাে + অন = পবন। লাে + অন = লবণ। |
| ঔ + অ = আবৃ + অ | পৌ + অক = পাবক। |
| ও + আ = অ + আ | গাে + আদি = গবাদি। |
| ও + এ = অ + এ | গাে + এষণা = গবেষণা। |
| ও + ই = অ + ই | পাে + ইত্র = পবিত্র |
| ঔ + ই = আবৃ + ই | নৌ + ইক = নাবিক। |
| ঔ + উ = আবৃ + উ | ভৌ + উক = ভাবুক |
২. ব্যঞ্জনসন্ধি
স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এদিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি
২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
৩, ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি
ক, চ, ট, ত, পৃ-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলাে যথাক্রমে গ, জ্ব, ডু (ড়), দৃ, বৃ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-
| ক্ + অ = গ | দিক্ + অন্ত =দিগন্ত। |
| চ্ + অ = জ | ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত। |
| ট্ + আ = ড় | ষট্ + আনন = ষড়ানন। |
| ত্ + অ = দ | তৎ + অবধি = তদবধি। |
| প + অ = ব | সুপ + অন্ত = সুবন্ত। |
| এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি। | |
২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যথা—
| অ + ছ = চ্ছ | এক + ছত্র = একচ্ছত্র |
| আ + ছ = চ্ছ | কথা + ছলে = কথাচ্ছলে |
| ই + ছ = চ্ছ | পরি + ছ = পরিচ্ছদ। |
| এরূপ – মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলােকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি। | |
৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
(ক) ১. ত্ ও দৃ-এর পর চূ ও ছ, থাকলে ত্ ও দৃ স্থানে চ হয়। যেমন—
| ত্ + চ = চ্চ | সৎ + চিন্তা =সচ্চিন্তা। |
| ত্ + ছ | উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ। |
| দ্ + চ = চ্চ | বিপদ + চয় = বিপচ্চয়। |
| দৃ + ছ = চ্ছ | বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া। |
| এরূপ — উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি। | |
২. ত্ ও দ্ এরপর জ্ব ও ঝ থাকলে ত্ ও দৃ-এর স্থানে জ্ব হয়। যেমন—
| ত্ + জ = জ্জ | সৎ + জন = সজ্জন। |
| দৃ + জ = জ্জ | বিপদ + জাল =বিপজ্জাল |
| ত্ + ঝ = দ্রু | কুৎ + ঝটিকা = কুক্কটিকা |
| এরূপ – উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি। | |
৩. ত্ ও দৃ-এরপর শ থাকলে ত্ ও দৃ-এর স্থলে চ্ এবং শ্-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন-
ত্ + শ = চ + ছ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস
এরূপ — চলচ্ছক্তি, উচ্ছঙ্খল ইত্যাদি।
৪. ত্ ও দৃ-এর পর ডু থাকলে ত্ ও দৃ এর স্থানে ড্র হয়। যেমন-
ত্ + ড = ডড় উৎ + ডীন = উড্ডীন।
এরূপ – বৃহড্ঢক্কা
৫. ত্ ও দৃ এর পর হ থাকলে ত্ ও দৃ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধূ হয়। যেমন-
ত্ + হ = দৃ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার।
দৃ + = দৃ + ধ = দ্ধ পদ + হতি = পদ্ধতি।
এরূপ – উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।
৬. ত্ ও দ, এর পর নৃ থাকলে ত্ ও -এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন
ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।
এরূপ – উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লম্ফন ইত্যাদি।
(খ) ১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনাে বর্গের অঘােষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনাে বর্গের ঘােষ অল্পপ্রাণ ও ঘােষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘােষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য ) জ), ঘােষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘােষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘােষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘােষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘােষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :
| ক্ + দ = গ + দ | বাক্ + দান = বাগদান |
| টু + য = ডু + য | ষ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র |
| ত্ + ঘ = দ্ + ঘ | উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন |
| ত্ + য = দৃ+ য | উৎ + যােগ = উদ্যোগ |
| ত্ + ব = দৃ + ব | উৎ +বন্ধন = উদ্বন্ধন। |
| ত্ + র = দৃ+ র | তৎ + রূপ = তদুপ |
| এরূপ -দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাল, সদ্গুরু, বাগদেবী ইত্যাদি। | |
২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘােষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘােষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্যধ্বনি হয়। যথা :
ক্ + ন = গ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগনির্ণয় বা দিনির্ণয়
ত্ + ম = দ/ন+ ম তৎ + মধ্যে = তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।
লক্ষণীয়: এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত। যেমন –
| বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, | জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। |
| তৎ + ময় = তন্ময়, | এরূপ—উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি। |
| মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, |
৩. ম্ এর পর যে কোনাে বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন—
| মৃ + ক = ঙ + ক্ | শম্ + ক =শঙ্কা। |
| ম্ + চ = ঞ + চ্ | সম্ + চয় = সঞ্চয়। |
| ম + ত = নৃ + ত্ | সম্ + তাপ = সন্তাপ। |
| এরূপ – কিম্ভূত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ন্যাস ইত্যাদি। | |
দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় মূ-এর পর কণ্ঠ্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে মৃ স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন-
| সম্ + গত = সংগত, |
| অহম্ + কার = অহংকার, |
| সম্ + খ্যা = সংখ্যা |
| এরূপ –সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংঘাত ইত্যাদি। |
৪. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, মৃ স্থলে অনুবার (ং) হয়। যেমন-
| সম্ + যম = সংযম, | সম্ + বাদ = সংবাদ, |
| সম্+ রক্ষণ = সক্ষণ | সম্ + লাপ = সংলাপ |
| সম্ + শয় = সংশয় | সম্ + সার = সংসার |
| সম্ + হার = সংহার। | |
| এরূপ-বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযােগ, সংযােজন, সংশােধন, সর্বংসহা, সয়ংবরা। | |
| ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)। | |
৫. চু ও জু-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –
চ + ন = চ + ঞ যাচ্ + না = যাচ্ঞা, রাজ্ + নী =রাজ্ঞী।
জ + ন = জ + ঞ, যজ্ + ন = যজ্ঞ,
৬. দৃ ও ধ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দৃ ও ধূ স্থলে অঘােষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন-
দ্> ত্ তদ্ + কাল = তৎকাল
ধূ > ত্ ক্ষুধ + পিপাসা =ক্ষুৎপিপাসা।
এরূপ —হৃৎকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।
৭. দৃ কিংবা ধূ-এর পরে স্ থাকলে, দৃ ও ধূ স্থলে অঘােষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন-
বিপদ + সংকুল = বিপৎসংকুল।
এরূপ — তৎসম।
৮. যু-এর পরে ত্ বা থু থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থু স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন
কৃষ + তি = কৃষ্টি, ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ।
বিসর্গ সন্ধি
সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত বৃ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘােষ উম্মধ্বনি অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঃ) রূপে লেখা হয়। র্ ও সূ বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :
১. র- জাত বিসর্গ ও
২. সৃ- জাত বিসর্গ।
১. র -জাত বিসর্গ : র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র- জাত বিসর্গ। যেমন:
অন্তর অন্তঃ, প্রাতরপ্রাতঃ, পুনর – পুনঃ ইত্যাদি।
২. স-জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্-জাত বিসর্গ। যেমন :
নমস্ – নমঃ, পুরস্ – পুরঃ, শিরস্ – শিরঃ ইত্যাদি।
বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।
বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয়:
১. বিসর্গ + স্বর এবং
২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।
১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি
অ-ধ্বনির পরস্থিত (অঘােষ উধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ও + অ – এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন-
ততঃ + অধিক = ততােধিক।
২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি
১. অ-কারের পরস্থিত স-জাত বিসর্গের পর ঘােষ অল্পপ্রাণ ও ঘােষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন –
| তিরঃ + ধান = তিরােধান, |
| মনঃ + ম = মনােরম, |
| মনঃ + হর = মনােহর, |
| তপঃ + বন = তপােবন ইত্যাদি। |
২. অ-কারের পরঙ্খিত রূ-জাত বিসর্গের পর উপযুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনােটি থাকলে বিসর্গ স্থানে ‘র’ হয়। যেমন—
| অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, |
| অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, |
| পুনঃ+ আয় = পুনরায়, |
| পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, |
| অহঃ + অহ = অহরহ। |
| এরূপ — পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতরুথান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তবর্তী ইত্যাদি। |
৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য ঘরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, বর্গীয় ঘােষ অল্পপ্রাণ ও ঘােষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব, হ-এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে ‘র’ হয়। যেমন-
| নিঃ + আকার = নিরাকার, |
| আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, |
| দুঃ + যােগ = দুর্যোগ ইত্যাদি। |
| এরূপ – নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লোভ, দুরন্ত ইত্যাদি। |
ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে ‘র’ এর সন্ধি হলে বিসর্গের লােপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী ব্ৰস ঘর দীর্ঘ হয়। যেমন –
নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।
৪. বিসর্গের পর অঘােষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘােষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘােষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘােষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘােষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমনঃ
| ঃ+ চ + ছ = শ + চ / ছ | নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ। |
| ঃ + ট /ঠ = ষ + ট | ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর। |
| ঃ + ত + থ = স + ত + থ | দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুস্থ। |
৫. অঘােষ অল্পপ্রাণ ও অঘােষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘােষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ হলে অঘোেষ মূর্ধন্য শিশূ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন-
| অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স + ক | নমঃ + কার = নমস্কার। |
| অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স + খ | পদঃ + খলন = পদখলন। |
| ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক | নিঃ + কর = নিষ্কর। |
| উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক | দুঃ + কর = দুষ্কর। |
| এরূপ – পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিস্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিস্কৃত, দুস্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি। | |
৬. কোনাে কোনাে ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লােপ হয় না। যেমন-
| প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল |
| মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট |
| শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া |
৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ত, স্থ কিংবা স পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লােপ পায়। যেমন—
| নিঃ + স্তন্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ। |
| দুঃ +থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ। |
| নিঃ + প = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ। |
সন্ধি বিচ্ছেদ এর উপরিউক্ত আলোচনা আপনার ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। ফাঁকি দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত ২১০টি সন্ধি বিচ্ছেদ ঝেড়ে ফেলুন।
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : নিপাতনে সিদ্ধ ও বিশেষ নিয়মে সাধিত | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ: নিপাতনে সিদ্ধ ও বিশেষ নিয়মে সাধিত |
| ১ | অক্ষৌহিণী = অক্ষ + ঊহিণী | ৭ | মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড |
| ২ | কুলটা = কুল + অটা | ৮ | রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ |
| ৩ | গবাক্ষ = গাে + অক্ষ | ৯ | শারঙ্গ = শার + অঙ্গ |
| ৪ | গবেন্দ্র = গাে + ইন্দ্র | ১০ | শুদ্ধোধন = শুদ্ধ + ওদন |
| ৫ | গবেশ্বর = গাে + ঈশ্বর | ১১ | সীমন্ত = সীমন + অত |
| ৬ | প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ় | ১২ | স্বৈর = স্ব + ঈর |
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ: নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ: নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গসন্ধি |
| ১ | অহর্নিশ = অহঃ + নিশ | ৫ | মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট |
| ২ | আস্পদ = আঃ + পদ | ৬ | শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া |
| ৩ | প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল | ৭ | হরিশ্চন্দ্র = হরিঃ + চন্দ্র |
| ৪ | বাচস্পতি = বাচঃ + পতি | ||
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ: নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ: নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি |
| ১ | আশ্চর্য = আ + চর্য | ৭ | পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি |
| ২ | একাদশ = এক + দশ | ৮ | পরস্পর = পর + পর |
| ৩ | গােস্পদ = গাে + পদ | ৯ | বনস্পতি = বন + পতি |
| ৪ | ঘােড়শ = ষ + দশ | ১০ | বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি |
| ৫ | তস্কর = তৎ + কর | ১১ | মনীষা = মনস + ঈষা |
| ৬ | দ্যুলােক = দিক্ + লােক | ১২ | ষােড়শ = ষট্ + দশ |
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি |
| ১ | অন্যান্য = অন্য + অন্য | ২ | শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন |
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি |
| ১ | উত্থান = উৎ + স্থান | ৫ | সংস্কার = সম + কার |
| ২ | উত্থাপন = উৎ + স্থাপন | ৬ | সংস্কৃত = সম + কৃত |
| ৩ | পরিকৃত = পরি + কৃত | ৭ | সংস্কৃতি = সুম + কৃতি |
| ৪ | পরিষ্কার = পরি + কার | ||
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : বিসর্গসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : বিসর্গসন্ধি |
| ১ | অতএব = অতঃ + এব | ২১ | দুস্থ = দুঃ + থ |
| ২ | অন্তর্লীন = অন্তঃ + লীন | ২২ | ধনুষ্টঙ্কার = ধনুঃ + টঙ্কার |
| ৩ | অহরহ = অহঃ + অহ | ২৩ | নিরাকার = নিঃ + আকার |
| ৪ | আবিষ্কার = আবিঃ + কার | ২৪ | নিশ্চয় = নিঃ + চয়ন |
| ৫ | আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ | ২৫ | নীরব = নিঃ + রব |
| ৬ | ইতস্তত = ইতঃ + তত | ২৬ | নীরস = নিঃ + রস |
| ৭ | চতুষ্কোণ = চতুঃ + কোণ | ২৭ | পুনরায় = পুনঃ +আয় |
| ৮ | যশােচ্ছা = যশঃ + ইচ্ছা | ২৮ | পুনর্জন্ম = পুনঃ + জন্ম |
| ৯ | যশােভিলাষ = যশঃ + অভিলাষ | ২৯ | প্রাতরাশ = প্রাতঃ+ আশ |
| ১০ | যশােলাভ = যশঃ + লাভ | ৩০ | পুরস্কার = পুরঃ + কার |
| ১১ | তিরস্কার = তিরঃ + কার | ৩১ | বহিষ্কার = বহিঃ + কার |
| ১২ | ততােধিক = ততঃ + অধিক | ৩২ | ভাস্কর = ভাঃ + কর |
| ১৩ | তপােধিক্য = তপঃ + আধিক্য | ৩৩ | ভ্রাতুস্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র |
| ১৪ | তপােবন = তপঃ + বন | ৩৪ | মনােজ = মনঃ + জ |
| ১৫ | দ্বিরাগমন = দ্বিঃ + আগমন | ৩৫ | মনােযােগ = মনঃ + যােগ |
| ১৬ | দুরাত্মা = দুঃ + আত্মা | ৩৬ | মনােহর = মনঃ + হর |
| ১৭ | দুর্যোগ = দুঃ + যােগ | ৩৭ | শিরােপরি = শিরঃ + উপরি |
| ১৮ | দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা | ৩৮ | শিরচ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ |
| ১৯ | দুর্লোভ = দুঃ + লােভ | ৩৯ | শ্রেয়স্কর = শ্রেয়ঃ + কর |
| ২০ | দুস্তর = দুঃ + তরকার | ||
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : ব্যঞ্জনসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : ব্যঞ্জনসন্ধি |
| ১ | অহংকার = অহম্ + কার | ৩১ | বাগলােপ = বাক্ + লােপ |
| ২ | উচ্চারণ = উৎ + চারণ | ৩২ | বাঙ্ময় = বাক্ + ময় |
| ৩ | উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস | ৩৩ | বিচ্ছেদ = বি + ছেদ |
| ৪ | উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল | ৩৪ | বুদ্ধ = বুধ + ত |
| ৫ | উডডীন = উৎ + ডীন | ৩৫ | বরঞ্চ = বরম্ + চ |
| ৬ | উদ্যোগ = উৎ + যােগ | ৩৬ | বসুন্ধরা = বসুম্ + ধরা |
| ৭ | উদ্যম = উৎ + যম | ৩৭ | মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি |
| ৮ | উদ্ধৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল | ৩৮ | রাজ্ঞী = রাজ + নী |
| ৯ | উদ্ধত = উৎ + হত | ৩৯ | শঙ্কা = শম্ + কান |
| ১০ | কিংবা = কিম্ + বা | ৪০ | শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র |
| ১১ | কিন্তু = কিম্ + তু | ৪১ | ষড়ঋতু = ষট + ঋতু |
| ১২ | কিন্নর = কিম্ + নর | ৪২ | ষড়ানন = ষট + আনন |
| ১৩ | কিম্ভুত = কিম্ + ভূত | ৪৩ | ষড়যন্ত্র = ষট + যন্ত্র |
| ১৪ | কুটিকা = কুৎ + ঝটিকা | ৪৪ | ষষ্ঠ = ষষ + থ |
| ১৫ | কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত | ৪৫ | সংখ্যা = সম্ + খ্যা |
| ১৬ | কৃষ্টি = কৃ + তি | ৪৬ | সংগত = সম + গত |
| ১৭ | ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ + পিপাসা | ৪৭ | সংঘ = সম্ + ঘ |
| ১৮ | চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র | ৪৮ | সংলাপ = সম্ + লাপ |
| ১৯ | জগন্নাথ = জগৎ + নাথ | ৪৯ | সিংহ = সিন্ + হ |
| ২০ | যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন | ৫০ | সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা |
| ২১ | যজ্ঞ = যজু + ন | ৫১ | সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র |
| ২২ | ণিজন্ত = ণিচ্ + অন্ত | ৫২ | সঞ্চয় = সম্ + চয় |
| ২৩ | দিগন্ত = দিক্ + অন্ত | ৫৩ | সদুপদেশ = সৎ + উপদেশ |
| ২৪ | পদ্ধতি = পদ্ + হতি | ৫৪ | সন্ধান = সম্ + ধান |
| ২৫ | পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ | ৫৫ | স্বয়ংবরা = স্বয়ম্ + বরা |
| ২৬ | প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা | ৫৬ | সুবন্ত = সুপ + অন্ত |
| ২৭ | বৃক্ষচ্ছায়া = বৃক্ষ-+ ছায়া | ৫৭ | সম্পল্লাভ = সম্পন্ + লাভ |
| ২৮ | বাগীশ = বাক্ + ঈশ | ৫৮ | সম্মান = সম্ + মান |
| ২৯ | বাগদত্তা = বাক্ + দত্তা | ৫৯ | সম্রাট = সম্ + রাট |
| ৩০ | বাগধারা = বাক্ + ধারা | ৬০ | হিংসা = হিন্ + সা |
| ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : স্বরসন্ধি | ক্রম | সন্ধি বিচ্ছেদ : স্বরসন্ধি |
| ১ | অত্যন্ত = অতি + অন্ত | ৩৭ | প্রত্যহ = প্রতি + অহ |
| ২ | অধমর্ণ = অধম + ঋণ | ৩৮ | পশ্বাচার = পশু + আচার |
| ৩ | অন্বেষণ = অনু + এষণ | ৩৯ | পশ্বধম = পশু + অধম |
| ৪ | অর্ধেক = অর্ধ + এক | ৪০ | বেশকম = বেশি + কম |
| ৫ | ইত্যাদি = ইতি + আদি | ৪১ | বধূক্তি = বধূ + উক্তি |
| ৬ | উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ | ৪২ | বধূৎসব = বধূ + উৎসব |
| ৭ | উপযুক্ত = উপরি + উক্ত | ৪৩ | ভয়ার্ত = ভয় + ঋত |
| ৮ | একেক = এক + এক | ৪৪ | ভবন = ভাে + অন |
| ৯ | একোন = এক + উন | ৪৫ | মাত্ৰাদেশ = মাতৃ + আদেশ |
| ১০ | একত্রিত = একত্র + ইত | ৪৬ | মাত্রুপদেশ = মাতৃ + উপদেশ |
| ১১ | কাঁচকলা = কাঁচা + কলা | ৪৭ | মিশকাল = মিশি + কাল |
| ১২ | কথােপকথন = কথা + উপকথন | ৪৮ | মতৈক্য = মত + ঐক্য |
| ১৩ | কথামৃত = কথা + অমৃত | ৪৯ | মন্বন্তর = মনু + অন্তর |
| ১৪ | ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত | ৫০ | মস্যাধার = মসী + আধার |
| ১৫ | গায়ক = গৈ + অক | ৫১ | মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য |
| ১৬ | গত্যন্তর = গতি + অন্তর | ৫২ | মহৌষধি = মহা + ওষধি |
| ১৭ | গবেষণা = গাে + এষণা | ৫৩ | রাজর্ষি = রাজা + ঋষি |
| ১৮ | চন্দ্রানন = চন্দ্র + আনন | ৫৪ | রত্নাকর = রত্ন + আকর |
| ১৯ | জনৈক = জন + এক | ৫৫ | রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র |
| ২০ | যথার্থ = যথা + অর্থ | ৫৬ | লঘূর্মি = লঘু + ঊর্মি |
| ২১ | যদ্যপি = যদি + অপি | ৫৭ | লবণ = লাে + অন |
| ২২ | তথৈবচ = তথা + এবচ | ৫৮ | শায়ন = শে + অন |
| ২৩ | তষী = তনু + ঈ | ৫৯ | শীতার্ত = শীত + ঋত |
| ২৪ | তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত | ৬০ | শতেক = শত + এক |
| ২৫ | ধর্মাধর্ম = ধর্ম + অধর্ম | ৬১ | শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা |
| ২৬ | নিন্দাহ = নিন্দা + অর্থ | ৬২ | সৃক্ত = সু + উক্ত |
| ২৭ | নীলােৎপল = নীল + উৎপল | ৬৩ | সানুনাসিক = স + অনুনাসিক |
| ২৮ | নদ্যম্বু = নদী + অষু | ৬৪ | স্বাধিকার = স + অধিকার |
| ২৯ | নদপকণ্ঠ = নদী + উপকণ্ঠ | ৬৫ | স্বাধীন = স্ব + অধীন |
| ৩০ | নবােঢ়া = নব + ঊঢ়া | ৬৬ | স্বেচ্ছা = স + ইচ্ছা |
| ৩১ | নরাধম = নর + অধম | ৬৭ | স্বল্প = সু + অল্প |
| ৩২ | নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র | ৬৮ | হিতােপদেশ = হিত + উপদেশ |
| ৩৩ | পিত্রালয় = পিতৃ + আলয় | ৬৯ | হিতৈষী = হিত + ঐষী |
| ৩৪ | পবিত্র = পাে + ইত্ৰ | ৭০ | হিমাচল = হিম + অচল |
| ৩৫ | পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা | ৭১ | হস্তান্তর = হস্ত + অন্তর |
| ৩৬ | প্রত্যেক = প্রতি + এক |

প্রশ্নঃ 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ------
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
তাপ একপ্রকার শক্তি যা আমাদের শরীরে ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি তৈরি করে। তাপগতিবিদ্যা অনুসারে, যখন দুটি বস্তুর মধ্যে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে আরেকটিতে শক্তি স্থানান্তরিত হয়, তখন প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা গরম হয় (অর্থাৎ, একটি অন্যটির চেয়ে বেশি তাপশক্তি অর্জন করে)। আর অন্যভাবে বলা যায়, তাপ হলো পদার্থের অণুগুলোর গতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন এক প্রকার শক্তি, যা কোনো বস্তু ঠান্ডা না গরম তার অনুভূতি জন্মায়। তাপগতিবিদ্যার তিনটি সূত্র রয়েছে ।
তাপ ও তাপমাত্রা একই বিষয় নয়। সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়। তাপমাত্রার পার্থক্যজনিত কারণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে, যেমন: পরিবহন, পরিচলন, বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপশক্তি গমন করে।
একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ বলে ।
যেমন- আগত – শব্দটির শুরুতে অন- উপসর্গটি যুক্ত হয়ে বিপরীত শব্দ হল- অনাগত ।
যেমন- অনুরাগ- শব্দটি রাগ- শব্দমূলের পূর্বে অনু- উপসর্গ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে, যেখানে অনু- উপসর্গটি ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করেছে । এখন অনু-র পরিবর্তে বি- উপসর্গ ব্যবহার করলে, বিরাগ- শব্দে বি-উপসর্গটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে, এবং শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায় । অর্থাৎ, ইতিবাচক অনু- উপসর্গের বদলে নেতিবাচক বি-উপসর্গের ব্যবহারে বিপরীত শব্দ গঠিত হল ।
যেমন- আজ – কাল, অতীত- ভবিষ্যত, অধম- উত্তম, ইত্যাদি ।
অ
|
অকর্মক |
সকর্মক |
অজ্ঞ |
প্রাজ্ঞ |
অধিত্যকা |
উপত্যকা |
|
অক্ষম |
সক্ষম |
অতিকায় |
ক্ষুদ্রকায় |
অনন্ত |
সান্ত |
|
অগ্র |
পশ্চাৎ |
অতিবৃষ্টি |
অনাবৃষ্টি |
অনুকূল |
প্রতিকূল |
|
অগ্রজ |
অনুজ |
অতীত |
ভবিষ্যত |
অনুগ্রহ |
নিগ্রহ |
|
অণু |
বৃহৎ |
অদ্য |
কল্য |
অগ্রজ |
অনুজ |
|
অচল |
সচল |
অধঃ |
ঊর্ধ্ব |
অনুরক্ত |
বিরক্ত |
|
অচলায়তন |
সচলায়তন |
অধম |
উত্তম |
অনুরাগ |
বিরাগ |
|
অচেতন |
সচেতন |
অধমর্ণ |
উত্তমর্ণ |
অনুলোম |
প্রতিলোম |
|
অলীক |
সত্য |
অশন |
অনশন |
অস্তগামী |
উদীয়মান |
|
অল্পপ্রাণ |
মহাপ্রাণ |
অসীম |
সসীম |
অস্তি |
নাস্তি/নেতি |
|
অহিংস |
সহিংস |
|
|
|
|
আ
|
আকর্ষণ |
বিকর্ষণ |
আধার |
আধেয় |
আরোহণ |
অবরোহণ |
|
আকুঞ্চন |
প্রসারণ |
আপদ |
সম্পদ |
আর্দ্র |
শুষ্ক |
|
আগত |
অনাগত |
আবশ্যক |
অনাবশ্যক |
আর্য |
অনার্য |
|
আগমন |
প্রস্থান |
আবশ্যিক |
ঐচ্ছিক |
আলস্য |
শ্রম |
|
আজ |
কাল |
আবাদি |
অনাবাদি |
আলো |
আঁধার |
|
আত্ম |
পর |
আবাহন |
বিসর্জন |
আশীর্বাদ |
অভিশাপ |
|
আত্মীয় |
অনাত্মীয় |
আবির্ভাব |
তিরোভাব |
আসক্ত |
নিরাসক্ত |
|
আদি |
অন্ত |
আবির্ভূত |
তিরোহিত |
আসামি |
ফরিয়াদী |
|
আদিম |
অন্তিম |
আবিল |
অনাবিল |
আস্তিক |
নাস্তিক |
|
আদ্য |
অন্ত্য |
আবৃত |
উন্মুক্ত |
আস্থা |
অনাস্থা |
ই
|
ইচ্ছুক |
অনিচ্ছুক |
ইদানীন্তন |
তদানীন্তন |
ইহকাল |
পরকাল |
|
ইতর |
ভদ্র |
ইষ্ট |
অনিষ্ট |
ইহলোক |
পরলোক |
|
ইতিবাচক |
নেতিবাচক |
|
|
ইহলৌকিক |
পারলৌকিক |
ঈ
|
ঈদৃশ |
তাদৃশ |
ঈষৎ |
অধিক |
|
|
উ
|
উক্ত |
অনুক্ত |
উত্তরায়ণ |
দক্ষিণায়ন |
উন্নত |
অবনত |
|
উগ্র |
সৌম্য |
উত্তাপ |
শৈত্য |
উন্নতি |
অবনতি |
|
উচ্চ |
নীচ |
উত্তীর্ণ |
অনুত্তীর্ণ |
উন্নীত |
অবনমিত |
|
উজান |
ভাটি |
উত্থান |
পতন |
উন্নয়ন |
অবনমন |
|
উঠতি |
পড়তি |
উত্থিত |
পতিত |
উন্মুখ |
বিমুখ |
|
উঠন্ত |
পড়ন্ত |
উদয় |
অস্ত |
উন্মীলন |
নিমীলন |
|
উৎকৃষ্ট |
নিকৃষ্ট |
উদ্ধত |
বিনীত/ নম্র |
উপকর্ষ |
অপকর্ষ |
|
উৎকর্ষ |
অপকর্ষ |
উদ্বৃত্ত |
ঘাটতি |
উপচয় |
অপচয় |
|
উৎরাই |
চড়াই |
উদ্যত |
বিরত |
উপকারী |
অপকারী |
|
উত্তম |
অধম |
উদ্যম |
বিরাম |
উপকারিতা |
অপকারিতা |
|
উত্তমর্ণ |
অধমর্ণ |
উর্বর |
ঊষর |
উপচিকীর্ষা |
অপচিকীর্ষা |
|
উত্তর |
দক্ষিণ |
উষ্ণ |
শীতল |
|
|
ঊ
|
ঊর্ধ্ব |
অধঃ |
ঊর্ধ্বগতি |
অধোগতি |
ঊষা |
সন্ধ্যা |
|
ঊর্ধ্বতন |
অধস্তন |
ঊর্ধ্বগামী |
অধোগামী |
ঊষর |
উর্বর |
ঋ
|
ঋজু |
বক্র |
|
|
|
|
এ
|
একান্ন |
পৃথগান্ন |
একাল |
সেকাল |
একূল |
ওকূল |
|
|
|
এখন |
তখন |
|
|
ঐ
|
ঐকমত্য |
মতভেদ |
ঐশ্বর্য |
দারিদ্র্য |
ঐহিক |
পারত্রিক |
|
ঐক্য |
অনৈক্য |
|
|
|
|
ও
|
ওস্তাদ |
সাকরেদ |
|
|
|
|
ঔ
|
ঔদার্য |
কার্পণ্য |
ঔচিত্য |
অনৌচিত্য |
ঔজ্জ্বল্য |
ম্লানিমা |
|
ঔদ্ধত্য |
বিনয় |
|
|
|
|
ক
|
কচি |
ঝুনা |
কুৎসিত |
সুন্দর |
কৃশাঙ্গী |
স্থূলাঙ্গী |
|
কদাচার |
সদাচার |
কুফল |
সুফল |
কৃষ্ণ |
শুভ্র/গৌর |
|
কনিষ্ঠ |
জ্যেষ্ঠ |
কুবুদ্ধি |
সুবুদ্ধি |
কৃষ্ণাঙ্গ |
শ্বেতাঙ্গ |
|
কপট |
সরল/অকপট |
কুমেরু |
সুমেরু |
কোমল |
কঠিন |
|
কপটতা |
সরলতা |
কুরুচি |
সুরুচি |
ক্রন্দন |
হাস্য |
|
কর্মঠ |
অকর্মণ্য |
কুলীন |
অন্ত্যজ |
ক্রোধ |
প্রীতি |
|
কল্পনা |
বাস্তব |
কুশাসন |
সুশাসন |
ক্ষণস্থায়ী |
দীর্ঘস্থায়ী |
|
কাপুরুষ |
বীরপুরুষ |
কুশিক্ষা |
সুশিক্ষা |
ক্ষীপ্র |
মন্থর |
|
কুঞ্চন |
প্রসারণ |
কৃতজ্ঞ |
অকৃতজ্ঞ/ কৃতঘ্ন |
ক্ষীয়মান |
বর্ধমান |
|
কুটিল |
সরল |
কৃপণ |
বদান্য |
|
|
|
কুৎসা |
প্রশংসা |
কৃশ |
স্থূল |
|
|
খ
|
খ্যাত |
অখ্যাত |
খুচরা |
পাইকারি |
খেদ |
হর্ষ |
|
খ্যাতি |
অখ্যাতি |
|
|
|
|
গ
|
গঞ্জনা |
প্রশংসা |
গূঢ় |
ব্যক্ত |
গৌণ |
মুখ্য |
|
গতি |
স্থিতি |
গুপ্ত |
প্রকাশিত |
গৌরব |
অগৌরব |
|
গদ্য |
পদ্য |
গৃহী |
সন্ন্যাসী |
গ্রামীণ |
নাগরিক |
|
গণ্য |
নগণ্য |
গ্রহণ |
বর্জন |
গ্রাম্য |
শহুরে |
|
গরল |
অমৃত |
গৃহীত |
বর্জিত |
গ্রাহ্য |
অগ্রাহ্য |
|
গরিমা |
লঘিমা |
গেঁয়ো |
শহুরে |
|
|
|
গরিষ্ঠ |
লঘিষ্ঠ |
গোপন |
প্রকাশ |
|
|
ঘ
|
ঘাটতি |
বাড়তি |
ঘাত |
প্রতিঘাত |
ঘৃণা |
শ্রদ্ধা |
চ
|
চক্ষুষ্মান |
অন্ধ |
চল |
অচল |
চিরায়ত |
সাময়িক |
|
চঞ্চল |
স্থির |
চলিত |
অচলিত/সাধু |
চ্যূত |
অচ্যূত |
|
চড়াই |
উৎরাই |
চিন্তনীয় |
অচিন্ত্য/অচিন্তনীয় |
|
|
|
চতুর |
নির্বোধ |
চুনোপুটি |
রুই-কাতলা |
|
|
ছ
|
ছটফটে |
শান্ত |
|
|
|
|
জ
|
জঙ্গম |
স্থাবর |
জল |
স্থল |
জোড় |
বিজোড় |
|
জড় |
চেতন |
জলে |
স্থলে |
জোয়ার |
ভাটা |
|
জটিল |
সরল |
জলচর |
স্থলচর |
জ্যোৎস্না |
অমাবস্যা |
|
জনাকীর্ণ |
জনবিরল |
জাতীয় |
বিজাতীয় |
জ্ঞাত |
অজ্ঞাত |
|
জন্ম |
মৃত্যু |
জাল |
আসল |
জ্ঞানী |
মূর্খ |
|
জমা |
খরচ |
জিন্দা |
মুর্দা |
জ্ঞেয় |
অজ্ঞেয় |
|
জরিমানা |
বকশিশ |
জীবন |
মরণ |
জ্যেষ্ঠা |
কনিষ্ঠা |
|
জাগ্রত |
ঘুমন্ত/সুপ্ত |
জীবিত |
মৃত |
|
|
|
জাগরণ |
ঘুম/সুপ্ত |
জৈব |
অজৈব |
|
|
ঠ
|
ঠুনকো |
মজবুত |
|
|
|
|
ড
|
ডুবন্ত |
ভাসন্ত |
|
|
|
|
ত
|
তদীয় |
মদীয় |
তারুণ্য |
বার্ধক্য |
তীক্ষ্ণ |
স্থূল |
|
তন্ময় |
মন্ময় |
তিমির |
আলোক |
তীব্র |
মৃদু |
|
তস্কর |
সাধু |
তিরস্কার |
পুরস্কার |
তুষ্ট |
রুষ্ট |
|
তাপ |
শৈত্য |
তীর্যক |
ঋজু |
ত্বরিত |
শ্লথ |
দ
|
দক্ষিণ |
বাম |
দুর্জন |
সুজন |
দৃঢ় |
শিথিল |
|
দণ্ড |
পুরস্কার |
দুর্দিন |
সুদিন |
দৃশ্য |
অদৃশ্য |
|
দাতা |
গ্রহীতা |
দুর্নাম |
সুনাম |
দেনা |
পাওনা |
|
দিবস |
রজনী |
দুর্বুদ্ধি |
সুবুদ্ধি |
দেশী |
বিদেশী |
|
দিবা |
নিশি/রাত্রি |
দুর্ভাগ্য |
সৌভাগ্য |
দোষ |
গুণ |
|
দিবাকর |
নিশাকর |
দুর্মতি |
সুমতি |
দোষী |
নির্দোষ |
|
দীর্ঘ |
হ্রস্ব |
দুর্লভ |
সুলভ |
দোস্ত |
দুশমন |
|
দীর্ঘায়ু |
স্বল্পায়ু |
দুষ্কৃতি |
সুকৃতি |
দ্বিধা |
নির্দ্বিধা/ দ্বিধাহীন |
|
দুঃশীল |
সুশীল |
দুষ্ট |
শিষ্ট |
দ্বৈত |
অদ্বৈত |
|
দুরন্ত |
শান্ত |
দূর |
নিকট |
দ্যুলোক |
ভূলোক |
|
দুর্গম |
সুগম |
দ্রুত |
মন্থর |
|
|
ধ
|
ধনাত্মক |
ঋণাত্মক |
ধারালো |
ভোঁতা |
ধূর্ত |
বোকা |
|
ধনী |
নির্ধন/দরিদ্র |
ধামির্ক |
অধার্মিক |
ধৃত |
মুক্ত |
|
ধবল |
শ্যামল |
|
|
|
|
ন
|
নতুন |
পুরাতন |
নিন্দা |
জাগরণ |
নির্মল |
মলিন |
|
নবীন |
নিন্দিত |
নিয়োগ |
বরখাস্ত |
নির্লজ্জ |
সলজ্জ |
|
নবীন |
প্রবীণ |
নিরক্ষর |
সাক্ষর |
নিশ্চয়তা |
অনিশ্চয়তা |
|
নর |
নারী |
নিরবলম্ব |
স্বাবলম্ব |
নীরস |
সরস |
|
নশ্বর |
অবিনশ্বর |
নিরস্ত্র |
সশস্ত্র |
নিশ্চেষ্ট |
সচেষ্ট |
|
নাবালক |
সাবালক |
নিরাকার |
সাকার |
নৈঃশব্দ্য |
সশব্দ |
|
নিঃশ্বাস |
প্রশ্বাস |
নির্দয় |
সদয় |
নৈতিকতা |
অনৈতিকতা |
|
নিকৃষ্ট |
উৎকৃষ্ট |
নির্দিষ্ট |
অনির্দিষ্ট |
নৈসর্গিক |
কৃত্তিম |
|
নিত্য |
অনিত্য |
নির্দেশক |
অনির্দেশক |
ন্যায় |
অন্যায় |
|
|
|
|
|
ন্যূন |
অধিক |
প
|
পক্ষ |
বিপক্ষ |
পূণ্যবান |
পূণ্যহীন |
প্রফুল্ল |
ম্লান |
|
পটু |
অপটু |
পুরস্কার |
তিরস্কার |
প্রবীণ |
নবীন |
|
পণ্ডিত |
মূর্খ |
পুষ্ট |
ক্ষীণ |
প্রবেশ |
প্রস্থান |
|
পতন |
উত্থান |
পূর্ণিমা |
অমাবস্যা |
প্রভু |
ভৃত্য |
|
পথ |
বিপথ |
পূর্ব |
পশ্চিম |
প্রশ্বাস |
নিঃশ্বাস |
|
পবিত্র |
অপবিত্র |
পূর্ববর্তী |
পরবর্তী |
প্রসন্ন |
বিষণ্ণ |
|
পরকীয় |
স্বকীয় |
পূর্বসূরী |
উত্তরসূরী |
প্রসারণ |
সংকোচন/আকুঞ্চন |
|
পরার্থ |
স্বার্থ |
পূর্বাহ্ণ |
অপরাহ্ণ |
প্রাচ্য |
প্রতীচ্য |
|
পরিকল্পিত |
অপরিকল্পিত |
প্রকাশিত |
অপ্রকাশিত |
প্রাচীন |
অর্বাচীন |
|
পরিশোধিত |
অপরিশোধিত |
প্রকাশ |
গোপন |
প্রতিকূল |
অনুকূল |
|
পরিশ্রমী |
অলস |
প্রকাশ্যে |
নেপথ্যে |
প্রায়শ |
কদাচিৎ |
|
পাপ |
পূণ্য |
প্রজ্জ্বলন |
নির্বাপণ |
প্রারম্ভ |
শেষ |
|
পাপী |
নিষ্পাপ |
প্রত্যক্ষ |
পরোক্ষ |
প্রীতিকর |
অপ্রীতিকর |
|
পার্থিব |
অপার্থিব |
প্রধান |
অপ্রধান |
|
|
ফ
|
ফলন্ত/ফলনশীল |
নিস্ফলা |
ফলবান |
নিস্ফল |
ফাঁপা |
নিরেট |
ব
|
বক্তা |
শ্রোতা |
বাধ্য |
অবাধ্য |
বিফল |
সফল |
|
বন্দনা |
গঞ্জনা |
বামপন্থী |
ডানপন্থী |
বিফলতা |
সফলতা |
|
বন্দী |
মুক্ত |
বাস্তব |
কল্পনা |
বিবাদ |
সুবাদ |
|
বদ্ধ |
মুক্ত |
বাল্য |
বার্ধক্য |
বিয়োগান্ত |
মিলনান্ত |
|
বন্ধন |
মুক্তি |
বাহুল্য |
স্বল্পতা |
বিয়োগান্তক |
মিলনান্তক |
|
বন্ধুর |
মসৃণ |
বাহ্য |
আভ্যন্তর |
বিরহ |
মিলন |
|
বন্য |
পোষা |
বিজেতা |
বিজিত |
বিলম্বিত |
দ্রুত |
|
বয়োজ্যেষ্ঠ |
বয়োকনিষ্ঠ |
বিদ্বান |
মূর্খ |
বিষাদ |
আনন্দ/ হর্ষ |
|
বরখাস্ত |
বহাল |
বিধর্মী |
স্বধর্মী |
বিস্তৃত |
সংক্ষিপ্ত |
|
বর্ধমান |
ক্ষীয়মান |
বিনয় |
ঔদ্ধত্য |
ব্যক্ত |
গুপ্ত |
|
বর্ধিষ্ণু |
ক্ষয়িষ্ণু |
বিনীত |
উদ্ধত |
ব্যর্থ |
সার্থক |
|
বহির্ভূত |
অন্তর্ভূক্ত |
বিপন্ন |
নিরাপদ |
ব্যর্থতা |
সার্থকতা |
|
বাদি |
বিবাদি |
বিপন্নতা |
নিরাপত্তা |
ব্যষ্টি |
সমষ্টি |
ভ
|
ভক্তি |
অভক্তি |
ভাটা |
জোয়ার |
ভূত |
ভবিষ্যত |
|
ভদ্র |
ইতর |
ভাসা |
ডোবা |
ভূমিকা |
উপসংহার |
|
ভীরু |
নির্ভীক |
ভোগ |
ত্যাগ |
ভেদ |
অভেদ |
ম
|
মঙ্গল |
অমঙ্গল |
মহাত্মা |
দুরাত্মা |
মুক্ত |
বন্দী |
|
মঞ্জুর |
নামঞ্জুর |
মানানসই |
বেমানান |
মুখ্য |
গৌণ |
|
মতৈক্য |
মতানৈক্য |
মান্য |
অমান্য |
মূর্খ |
জ্ঞানী |
|
মসৃণ |
খসখসে |
মিতব্যয়ী |
অমিতব্যয়ী |
মূর্ত |
বিমূর্ত |
|
মহৎ |
নীচ |
মিথ্যা |
সত্য |
মৌখিক |
লিখিত |
|
মহাজন |
খাতক |
মিলন |
বিরহ |
মৌলিক |
যৌগিক |
য
|
যত্ন |
অযত্ন |
যুদ্ধ |
শান্তি |
যৌথ |
একক |
|
যশ |
অপযশ |
যোগ |
বিয়োগ |
যৌবন |
বার্ধক্য |
|
যুক্ত |
বিযুক্ত |
যোগ্য |
অযোগ্য |
|
|
|
যুগল |
একক |
যোজন |
বিয়োজন |
|
|
র
|
রক্ষক |
ভক্ষক |
রাজি |
নারাজ |
রোদ |
বৃষ্টি |
|
রমণীয় |
কুৎসিত |
রুগ্ন |
সুস্থ |
রোগী |
নিরোগ |
|
রসিক |
বেরসিক |
রুদ্ধ |
মুক্ত |
|
|
|
রাজা |
প্রজা |
রুষ্ট |
তুষ্ট |
|
|
ল
|
লঘিষ্ঠ |
গরিষ্ঠ |
লাজুক |
নির্লজ্জ |
লেন |
দেন |
|
লঘু |
গুরু |
লেজ |
মাথা |
লেনা |
দেনা |
|
লব |
হর |
লৌকিক |
অলৌকিক |
|
|
শ
|
শঠ |
সাধু |
শিষ্ট |
অশিষ্ট |
শুষ্ক |
সিক্ত |
|
শঠতা |
সাধুতা |
শিষ্য |
গুরু |
শূণ্য |
পূর্ণ |
|
শায়িত |
উত্থিত |
শীত |
গ্রীষ্ম |
শোভন |
অশোভন |
|
শয়ন |
উত্থান |
শীতল |
উষ্ণ |
শ্বাস |
প্রশ্বাস |
|
শারীরিক |
মানসিক |
শুক্লপক্ষ |
কৃষ্ণপক্ষ |
শ্রী |
বিশ্রী |
|
শালীন |
অশালীন |
শুচি |
অশুচি |
শ্লীল |
অশ্লীল |
|
শাসক |
শাসিত |
শুদ্ধ |
অশুদ্ধ |
|
|
|
শিক্ষক |
ছাত্র |
শুভ্র |
কৃষ্ণ |
|
|
স
|
সংকীর্ণ |
প্রশস্ত |
সদৃশ |
বিসদৃশ |
সাহসিকতা |
ভীরুতা |
|
সংকোচন |
প্রসারণ |
সধবা |
বিধবা |
সিক্ত |
শুষ্ক |
|
সংকুচিত |
প্রসারিত |
সন্ধি |
বিগ্রহ |
সুকৃতি |
দুষ্কৃতি |
|
সংক্ষিপ্ত |
বিস্তৃত |
সন্নিধান |
ব্যবধান |
সুগম |
দুর্গম |
|
সংক্ষেপ |
বিস্তার |
সফল |
বিফল |
সুন্দর |
কুৎসিত |
|
সংক্ষেপিত |
বিস্তারিত |
সবল |
দুর্বল |
সুদর্শন |
কুদর্শন |
|
সংগত |
অসংগত |
সবাক |
নির্বাক |
সুধা |
জাগ্রত |
|
সংযত |
অসংযত |
সমতল |
অসমতল |
সুপ্ত |
জাগ্রত |
|
সংযুক্ত |
বিযুক্ত |
সমষ্টি |
ব্যষ্টি |
সুয়ো |
দুয়ো |
|
সংযোগ |
বিয়োগ |
সমাপিকা |
অসমাপিকা |
সুশীল |
দুঃশীল |
|
সংযোজন |
বিয়োজন |
সমাপ্ত |
আরম্ভ |
সুশ্রী |
কুশ্রী |
|
সংশ্লিষ্ট |
বিশ্লিষ্ট |
সম্পদ |
বিপদ |
সুষম |
অসম |
|
সংশ্লেষণ |
বিশ্লেষণ |
সম্প্রসারণ |
সংকোচন |
সুসহ |
দুঃসহ |
|
সংহত |
বিভক্ত |
সম্মুখ |
পশ্চাত |
সুস্থ |
দুস্থ |
|
সংহতি |
বিভক্তি |
সরব |
নিরব |
সূক্ষ্ম |
স্থূল |
|
সকর্মক |
অকর্মক |
সরল |
কুটিল/জটিল |
সৃষ্টি |
ধ্বংস |
|
সকাল |
বিকাল |
সশস্ত্র |
নিরস্ত্র |
সৌখিন |
পেশাদার |
|
সক্রিয় |
নিষ্ক্রিয় |
সস্তা |
আক্রা |
সৌভাগ্যবান |
দুর্ভাগ্যবান/ভাগ্যহত |
|
সক্ষম |
অক্ষম |
সসীম |
অসীম |
স্তুতি |
নিন্দা |
|
সচল |
নিশ্চল |
সহযোগ |
অসহযোগ |
স্তাবক |
নিন্দুক |
|
সচেতন |
অচেতন |
সহিষ্ণু |
অসহিষ্ণু |
স্থাবর |
জঙ্গম |
|
সচেষ্ট |
নিশ্চেষ্ট |
সাঁঝ |
সকাল |
স্থলভাগ |
জলভাগ |
|
সচ্চরিত্র |
দুশ্চরিত্র |
সাকার |
নিরাকার |
স্নিগ্ধ |
রুক্ষ |
|
সজাগ |
নিদ্রিত |
সাক্ষর |
নিরক্ষর |
স্বনামী |
বেনামী |
|
সজ্জন |
দুর্জন |
সাদৃশ্য |
বৈসাদৃশ্য |
স্বর্গ |
নরক |
|
সজ্ঞান |
অজ্ঞান |
সাফল্য |
ব্যর্থতা |
স্বাতন্ত্র্য |
সাধারণত্ব |
|
সঞ্চয় |
অপচয় |
সাবালক |
নাবালক |
স্বাধীন |
পরাধীন |
|
সতী |
অসতী |
সাবালিকা |
নাবালিকা |
স্বার্থপর |
পরার্থপর |
|
সত্বর |
ধীর |
সাম্য |
বৈষম্য |
স্মৃতি |
বিস্মৃতি |
|
সদয় |
নির্দয় |
সার |
অসার |
স্থির |
অস্থির |
|
সদর |
অন্দর |
সার্থক |
নিরর্থক |
|
|
|
সদাচার |
কদাচার |
সাহসী |
ভীরু |
|
|
হ
|
হরণ |
পূরণ |
হাল |
সাবেক |
হৃদ্যতা |
শত্রুতা |
|
হর্ষ |
বিষাদ |
হালকা |
ভারি |
হ্রস্ব |
দীর্ঘ |
|
হাজির |
গরহাজির |
হিত |
অহিত |
হ্রাস |
বৃদ্ধি |
|
হার |
জিত |
হিসেবি |
বেহিসেবি |
|
|

প্রশ্নঃ 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন।
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
বিশেষ্য পদ
যে পদে সাধারণত কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সমষ্টি, বিষয়, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় বা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে । যেমন-সুন্দর (বিশেষ্য) মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে। সুন্দর (বিশেষ্য) মানুষকে নিজের দিকে টানে।
বিশেষ্য পদের প্রকারভেদ : বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার | মথা-
বিশেষণ পদ
যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে । যেমন- তিনটি বছর। এ যে আমাদের চেনা লোক । সন্তানের প্রতি মাতৃন্রেহ আন্তরিক।
বিশেষণ পদের প্রকারভেদ : বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা- নাম নিশেষণ ও ভাব
বিশেষণ ।

প্রশ্নঃ কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম আছে?
Best One ব্যাখ্যা যোগ করুন।বর্ণনাঃ
সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ যদি একই ধাতু বা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত হয়, তবে তাকে সমধাতুজ কর্মপদ বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই শব্দমূল থেকে গঠিত হলে তাকে সমধাতুজ কর্মপদ বলে। যেমন-
আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি।
এখানে ক্রিয়াপদ ‘ঘুমিয়েছি’, আর কর্মপদ ‘ঘুম’ (কী ঘুমিয়েছি?)। আর এই ‘ঘুমিয়েছি’ আর ‘ঘুম’ দুটি শব্দেরই শব্দমূল ‘ঘুম্’। অর্থাৎ, শব্দ দুইটি একই ধাতু হতে গঠিত (ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে)। সুতরাং, এই বাক্যে ‘ঘুম’ কর্মটি একটি সমধাতুজ কর্ম। এরকম-
আজ কী খেলা খেললাম। (খেল্)
আর মায়াকান্না কেঁদো না। (কাঁদ্)

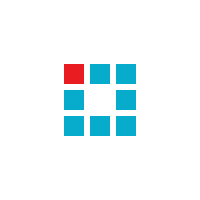
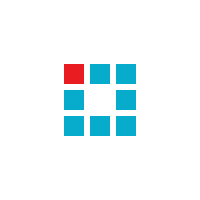
দুঃখিত । আপনি লগ ইন করেন নি। কোন প্রশ্ন কে পরিবর্তন করার জন্য প্রথমে আপনাকে লগ ইন করতে হবে।
বিষয়ভিত্তিক সমাধান
প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমাধান
অনলাইন মডেল টেস্ট
আমাদের সিস্টেম ডেভেলপারগণ এই অপশন নিয়ে কাজ করছে । আগামী ৩১ September অপশনটি শুভ উদ্বোধন করা হবে।
আর মাত্র
বাকি
আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ